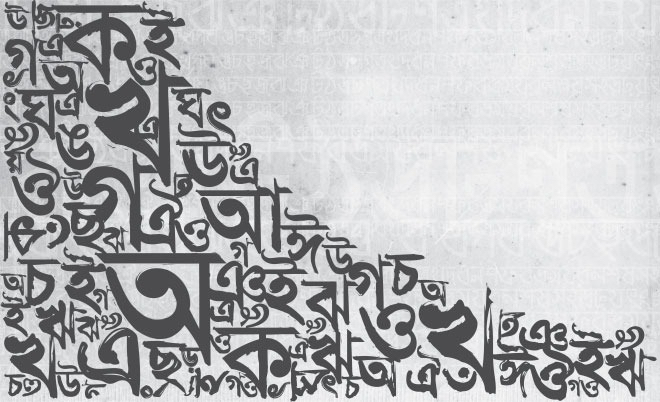
প্রাচীন বাংলার ভাষাতত্ত্ব: হাজার বছর আগের বাংলা ভাষার তত্ত্বতালাশ
(১)
১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবারের পুঁথিশালা থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কার করলেন চর্যাপদ সমূহের একটি সংকলন। আবিষ্কারের দশ বছরের মাথায় তাঁর সম্পাদনায় ১৯১৬ সালে সেগুলি প্রকাশিত হল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে। তারপর থেকে এর ভাষা ও বিষয়বস্তু নিয়ে, চর্যার পদকর্তাদের নিয়ে অনেক গবেষণা হল। আলাপ আলোচনা ও বিতর্কের দীর্ঘ ইতিহাস পেরিয়ে প্রাচীনতম বাংলা ভাষার প্রায় একমাত্র এই নিদর্শনের নানাদিক আমাদের কাছে এখন অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বৌদ্ধধর্মের বিশেষজ্ঞ আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী, চর্যাপদের তিব্বতী টীকার আবিষ্কর্তা প্রবোদ চন্দ্র বাগচী ছাড়াও যে সমস্ত ভাষাতাত্ত্বিকের গবেষণা এই কাজে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মহম্মদ শহীদুল্লাহ, আচার্য সুকুমার সেন, অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক রামেশ্বর শ, অধ্যাপক নির্মল দাশ প্রমুখ।
বাংলা ভাষার প্রাচীনতম রূপটির বিস্তারিত পরিচয় জানার আগে বাংলা ভাষা কীভাবে ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে বিবর্তনসূত্রে জন্ম নিল সেই সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা বলা প্রয়োজন। ১৭৮৬ সালে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে তার তৃতীয় বার্ষিক বক্তৃতার সময় স্যর উইলিয়ম জোন্স একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র সবার চোখের সামনে আনেন। সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন এবং আধুনিক ভারতীয় ও আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে মিলের এই কথাটি ধরে এরপর শুরু হল ব্যাপক গবেষণা। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান ও তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান জার্মানি সহ নানা দেশে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে চর্চিত হতে লাগল। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভাষাতাত্ত্বিক সূত্র আবিষ্কৃত হল। জানা গেল উত্তর ভারত, ইরান ও ইউরোপের অনেকগুলি ভাষা একটি প্রত্ন ভাষা থেকে নানা শাখা উপশাখার অনেক স্তর পেরিয়ে জন্ম নিয়েছে। এই প্রত্ন ভাষাটির নাম দেওয়া হল ইন্দো ইউরোপীয়। এই ভাষায় যারা কথা বলত তাঁদের বলা হয় ইন্দো ইউরোপীয় জনগোষ্ঠী।
এই ইন্দো ইউরোপীয়রা ছিল যাযাবর। ক্রমশ তারা ছড়িয়ে পড়ল নানা দিকে। সেইসঙ্গে ক্রমশ তাঁদের ভাষায় এলো পরস্পরের থেকে অনেকখানি বদল। একসময়ে যেগুলি ছিল প্রত্ন ইন্দো ইউরোপীয় ভাষার উপভাষা, সেগুলিই ধীরে ধীরে এক একটি স্বতন্ত্র ভাষা হয়ে উঠল। প্রত্ন ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাটির কোনও নিদর্শন আমরা পাই নি। কিন্তু এই ভাষাটিকে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার সাহায্যে পুনঃনির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে।
ইন্দো ইউরোপীয় ভাষার বিবর্তনের এই পর্বটিকে সহজ করে বুঝতে গেলে কিছু জটিলতা এড়িয়ে যেতে হয়। কিছু বিতর্ককেও পাশে সরিয়ে রাখতে হয়। যেমন ধরা যাক হিত্তীয় ভাষাটির কথা। একসময়ে মনে করা হত ইন্দো ইউরোপীয় থেকে যে দশটি আলাদা শাখার জন্ম হয়েছে হিত্তীয় তারই একটি। কিন্তু পরে আরো এমন কিছু প্রমাণ পাওয়া গেল, এমন কিছু গবেষণা হল যে এখন অনেকেই মনে করেন প্রত্ন ইন্দো ইউরোপীয় যেমন একটি ভাষা, হিত্তীয়ও তেমনি আলাদা একটি ভাষা। কোনও এক জননী ভাষা থেকে প্রত্ন ইন্দো ইউরোপীয় ও হিত্তীয় এই দুই ভাষার জন্ম হয়েছে। কেন এই চিন্তাভাবনার বদল সে সব কথা বলতে গেলে ভাষাতত্ত্বের জটিল আলোচনায় ঢুকতে হবে। আমরা সেই তাত্ত্বিক জটিলতায় এখানে যাব না। প্রথাগত ধারণা অনুযায়ী হিত্তীয়কে প্রত্ন ইন্দো ইউরোপীয়র একটি শাখা বলেই ধরে নেব।
ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাটি কালের নিয়মে দশটি শাখায় ভাগ হয়ে গেল। এই দশটি শাখাকে আবার দুটি বড় গোষ্ঠীর মধ্যে প্রথমে ভাগ করে রাখা হয়। একটি গোষ্ঠীতে থাকে চারটি ভাষা। অন্য গোষ্ঠীতে বাকি ছয়টি ভাষা। একটি গোষ্ঠীর নাম দেওয়া হয়েছে কেন্তুম গোষ্ঠী। অপরটির নাম দেওয়া হয়েছে সতম গোষ্ঠী। এইরকম নামকরণ কেন তা একটু বলা যাক। একটি প্রত্ন ইন্দো ইউরোপীয় ধ্বনি চারটি ভাষায় স হিসেবে উচ্চারিত হয় – ঐগুলি সতম গোষ্ঠীর ভাষা। আর ছটি ভাষায় ক হিসেবে উচ্চারিত হয়। সেগুলো কেন্তুম গোষ্ঠীর ভাষা। ইংরাজী হান্ড্রেড বা বাংলার একশো শব্দটির যা মানে, কেন্তুম ও সতম শব্দদুটির অর্থও তাই।
কেন্তুম গোষ্ঠীর মধ্যে যে ছটি শাখা পড়ে সেগুলি হল – গ্রীক, ইতালিক, কেলতিক, টিউটনিক বা জার্মানিক, তোখারীয়, হিত্তীয়*। আগে উল্লিখিত বিতর্কের কথা মাথায় রেখে আমরা হিত্তীয়র পাশে একটি * চিহ্ন জুড়ে দিয়েছি।
সতম গোষ্ঠীর মধ্যে যে চারটি শাখা পড়ে সেগুলি হল ইন্দো ইরানীয়, বালতো স্লাবিক, আলবেনীয়, আর্মেনীয়।
এই দশটি শাখার কোনটি থেকে পরবর্তীকালে কোন কোন বিখ্যাত ও সুপরিচিত ভাষা এসেছে সেগুলি আমরা একটু দেখেনি একটা তালিকা তৈরি করে। এখানে যেটা বলার এই ভাষাগুলির বাইরে আরো অনেক ভাষা এই শাখাগুলি থেকে এসেছে। আমরা কয়েকটির কথাই মাত্র এখানে উল্লেখ করলাম।
ইন্দো ইরানীয় – বৈদিক, সংস্কৃত, বিভিন্ন প্রাকৃত, পালি, বিভিন্ন উত্তর মধ্য পশ্চিম ও পূর্ব ভারতীয় ভাষা যেমন বাংলা, হিন্দি, উর্দু, মারাঠী, পাঞ্জাবী, গুজরাতি, অসমীয়া, ওড়িয়া, ভোজপুরী, মৈথিলী ইত্যাদি।
এছাড়া ইরান বা পারস্যের প্রাচীন ভাষা আবেস্তীয় ও আধুনিক ভাষা ফারসী ইন্দো ইরানীয় উৎস থেকে এসেছে।
বালতো স্লাবিক – রুশ, বুলগেরীয়, লিথুয়নীয়।
আলবেনীয় – আধুনিক আলবেনিয়ান
আর্মেনীয় – আধুনিক আর্মেনিয়ান
গ্রীক – ধ্রুপদী গ্রীক, আধুনিক গ্রীক
ইতালিক – লাতিন, ফরাসী, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ
কেলতিক – আইরিশ
টিউটনিক বা জার্মানিক – ইংরাজী, জার্মান, ডাচ বা ওলন্দাজ
তোখারীয় – প্রাচীন তোখারীয়। এই শাখাটি থেকে কোনও আধুনিক ভাষার জন্ম হয় নি। বর্তমানে লুপ্ত।
হিত্তীয় – এশিয় মাইনর অঞ্চলে প্রাচীনকালে এই ভাষাটি প্রচলিত ছিল। এর কোনও আধুনিক রূপ নেই। এটি ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যায়।
ওপরে উল্লিখিত প্রাচীন দশটি শাখার আলাদা আলাদা বিবর্তনপথ আছে। সেগুলির মধ্যে ইন্দো ইরানীয় ভাষার বিবর্তন পথটি নিয়েই আমরা কথা বলব। কারণ এই বিবর্তন পথেই বাংলা সহ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাগুলিকে আমরা পাব।
ইন্দো ইরানীয় শাখাটি মূল ইন্দো ইউরোপীয় থেকে কবে আলাদা হয়ে গিয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। অনুমান করা হয় সেটা আজ থেকে চার, সাড়ে চার হাজার বছর আগে হয়ে থাকবে। ইন্দো ইরানীয় ভাষাটি আবার তিনটি শাখায় ভাগ হয়ে গেল আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে। একটি শাখা থেকে গেল ইরানে। সেখান থেকেই এল জেন্দ আবেস্তার ভাষা আবেস্তান। একটি শাখা চলে এল কাশ্মীরে। সেখানকার ভাষাটির নাম হল দরদীয়। এই ভাষা থেকে আধুনিক কাশ্মীরী ভাষা জন্ম নিয়েছে। আর একটি শাখা আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে ভারতের মূল ভূখণ্ডে চলে এল এবং সেই শাখাটির নাম হল ইন্দো আর্য।
এই ইন্দো আর্য বা ভারতীয় আর্য ভাষাটির প্রাচীনতম নিদর্শনটিতে লেখা হল ঋকবেদ। এই প্রাচীন ইন্দো আর্য বা ওল্ড ইন্দো এরিয়ানকে তাই বৈদিক ভাষা নামেও ডাকা হয়। এর অপর একটি পরিচিত নাম হল বৈদিক সংস্কৃত। এই নামটি ঠিক ভাষাতত্ত্ব সমর্থিত নয়, কারণ সংস্কৃত ভাষাটি বৈদিকের ই এক বিশেষ ধরন। কিন্তু এই নামটি বিশেষ জনপ্রিয় এবং বিভিন্ন মান্য বইপত্রেও এই নামটি খুবই পাওয়া যায় বলে এর উল্লেখ করে রাখা দরকার।
ভারতবর্ষ বিশাল দেশ। আর্যভাষীরাও একজায়গায় আবদ্ধ থাকল না। তারাও ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল এই দেশের নানা দিকে। বিশেষ করে লোহার আবিষ্কারের পর লোহার হাতিয়ারের ওপর ভর করে দা কুড়ুল দিয়ে বন জঙ্গল কেটে তারা অনেক নতুন নতুন জনপদে এসে পৌঁছল। এই ভৌগোলিক বিস্তারের সূত্র ধরে ভারতীয় আর্য ভাষার মধ্যেই চারটি আলাদা উপভাষার জন্ম হল। এগুলি হল প্রাচ্য, উদীচ্য, মধ্যদেশীয়, দাক্ষিণাত্য।
কালগত দিক থেকে ভারতীয় আর্যভাষাকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়।
প্রাচীন ভারতীয় আর্য – খ্রিস্ট পূর্বাব্দ ১৫০০ থেকে খ্রিস্ট পূর্বাব্দ ৬০০
মধ্যভারতীয় আর্য – খ্রিস্ট পূর্বাব্দ ৬০০ থেকে ৯০০ খ্রিস্টাব্দ
নব্য ভারতীয় আর্য – ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে আধুনিক কাল
প্রাচীন ভারতীয় আর্যর যেমন চারটি শাখা ছিল তেমনি মধ্যভারতীয় আর্যর ছিল পাঁচটি শাখা। এই পর্বের ভাষা কালের নিয়মে অনেক বদলেছে লোকের মুখে মুখে। বদলে যাওয়া ভাষার নাম হয়েছে প্রাকৃত। প্রাকৃতের পাঁচটি আঞ্চলিক বিভাগ ছিল –
মাগধী প্রাকৃত
অর্ধমাগধী প্রাকৃত
পৈশাচী প্রাকৃত
শৌরসেনী প্রাকৃত
মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত
এই মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার পর্বেই দুটি অত্যন্ত পরিচিত ভাষা দুটি আলাদা আলাদা দৃষ্টিকোণ ও ভাষাদর্শন থেকে জন্ম নিল। একটি হল সংস্কৃত আর একটি হল পালি। এই প্রসঙ্গে এই দুটো ভাষার কথা একটু বলা যাক।
প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা বা বৈদিক ভাষায় বেদ লেখা হয়েছে। এই ভাষা মানুষের কাছে তাই অত্যন্ত পবিত্র। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মেই কালের বদলের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা বদলে যায়। পবিত্র ভাষাটি লোকমুখে বদলে যাচ্ছে, লোকে ধর্মকে বলছে ধম্ম, আর্যকে বলছে অজ্জ, কৃষ্ণকে বলছে কান্হ – এসব অনেকের একেবারেই পছন্দ হল না। তাঁরা ভাবতে থাকলেন কীভাবে এই “বিকৃতি” রোধ করা যায়। তাঁদের নিয়ম কানুন তৈরি করার কথা মনে হল। কোন শব্দের উচ্চারণ কীভাবে করতে হবে, কোন শব্দ কীভাবে কার পরে ব্যবহার করতে হবে, শব্দর সঙ্গে শব্দ বা শব্দাংশ যুক্ত করার পদ্ধতি কী হবে – এই সব কিছুই তাঁরা নির্দিষ্ট নিয়মে বেঁধে ভাষার বিকৃতি রোধ করতে চাইলেন। এই নিয়ম যারা বিভিন্ন যুগে লিখলেন তাঁদের বলা হয় বৈয়াকরণ। ভারতীয় বৈয়াকরণদের তালিকা লম্বা। সবার সব বইপত্র আমরা পাইওনি। তবে এই নিয়ম রচয়িতাদের মধ্যে বিখ্যাত ত্রয়ী হলেন পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি।
প্রাচীন ভারতের ভাষাচিন্তার কথা উঠলেই যাঁর নাম সবার প্রথমে মাথায় আসে তিনি হলেন পাণিনি। তাঁর সময়কালটি নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। আনুমানিক খ্রিস্ট পূর্বাব্দ পঞ্চম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে তাঁর লেখা অষ্টাধ্যায়ী সেকালে যেমন প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল, তেমনি একালেও বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদের মধ্যে দিয়ে আন্তর্জাতিক ভাষাচর্চায় তা প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পাণিনির আগেই শব্দ উৎস সন্ধান করে যাস্ক লিখেছিলেন তাঁর নিরুক্ত। অন্যান্য নিরুক্তকারদের রচনা আমরা পাই নি। পাণিনির পরে ভারতীয় ব্যাকরণ চর্চায় যে দুই বিখ্যাত ভাষাচিন্তকের নাম আমরা পাই তাঁরা হলেন খ্রিস্ট পূর্বাব্দ তৃতীয় শতাব্দীর কাত্যায়ন এবং খ্রিস্ট পূর্বাব্দ দ্বিতীয় শতকের পতঞ্জলি। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে যে পরিণত ব্যাকরণচিন্তার প্রকাশ আমরা দেখি সেখান থেকে সহজেই বোঝা যায় এর আগে অনেকদিন ধরেই ভারতে ব্যাকরণ চর্চার ধারাটি বিকশিত হয়ে উঠছিল।
পাণিনির প্রায় দুই শতাব্দী পরের খ্রিস্ট পূর্বাব্দ তৃতীয় শতকের ব্যাকরণবিদ ছিলেন কাত্যায়ন। সেই সময় ভাষার প্রবাহ আরো বদলে গিয়েছিল এবং সেইজন্য কাত্যায়ন পাণিনির বেশ কিছু সূত্রকে সংশোধন করার প্রয়োজন মনে করেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। কাত্যায়নের রচনার নাম বার্তিক। পাণিনির দেড় হাজার সূত্রকে তিনি সংশোধন করেছিলেন।
কাত্যায়নের প্রায় এক শতাব্দী পরে সংস্কৃত ব্যাকরণের আর এক বিশিষ্ট লেখক পতঞ্জলির আবির্ভাব হয় খ্রিস্ট পূর্বাব্দ দ্বিতীয় শতকে। পতঞ্জলির মহাভাষ্য কোনও মৌলিক রচনা নয়, পাণিনির ব্যাকরণের এক অসামান্য ভাষ্য। পাণিনির অনেক সূত্রকে কাত্যায়ন খণ্ডন করেছিলেন। পতঞ্জলি কাত্যায়নের সূত্রগুলিকে খণ্ডন করে আবার পাণিনির সূত্রগুলিকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। পাণিনির ব্যাকরণের মতোই পতঞ্জলির মহাভাষ্যও আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। পতঞ্জলির ব্যাকরণ রচনা শুধু বিশ্লেষণের দিক থেকে বিশিষ্ট নয়, রচনারীতির দিক থেকে সরস ও প্রাঞ্জল বলে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল।
সংস্কৃত ভাষা কীভাবে জন্ম নিল, কীভাবে কারা তার নিয়ম তৈরি করলেন সেই কথার পর চলে আসি পালি ভাষার প্রসঙ্গে। সংস্কৃতের মতো এই ভাষাটিও তৈরি করতে হয়েছিল। তবে এটি তৈরি হয়েছিল একেবারে অন্য এক দর্শন থেকে। সংস্কৃত ভাষার নির্মাতারা চাইছিলেন লোকমুখে বেদের ভাষার বিকৃতি রোধ করতে। আর পালি ভাষার নির্মাতারা চাইছিলেন লোকের মুখের ভাষাকে তাঁদের মতবাদ প্রচারের কাজে আরো দৃঢ়ভাবে ব্যবহার করতে।
পালি ভাষার উদ্ভবের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের তথা প্রতিবাদী আন্দোলনের নিবিড় সম্পর্কের কথা সবাই জানেন। বৌদ্ধ ধর্ম বৈদিক ধর্ম থেকে অন্যভাবে ভেবেছিল ও লোকেরা যে ভাষা বলছে সেই প্রাকৃত ভাষাতেই তাদের ধর্ম বা ধম্ম প্রচার করে তাকে জনপ্রিয় করতে চাইছিল। কিন্তু বিরাট ভারতে প্রাকৃতের তখন বেশ কয়েকটি আলাদা আলাদা রূপ। এগুলির মধ্যেকার পারস্পরিক দূরত্বকে অতিক্রম করে একটি মান্য প্রাকৃত ভাষা তৈরি করার দরকার পড়ল ‘ধম্ম’ প্রচারের জন্য। যেটা ঠিক কারোর ই মাতৃভাষা নয়, কিন্তু যে ভাষা সব অঞ্চলের সাধারণ মানুষই মোটামুটি বুঝতে পারেন।
আজকের দিনেও আমরা লেখালিখির ক্ষেত্রে, স্কুল কলেজের বইপত্র তৈরির ক্ষেত্রে এই মান্য ভাষা ব্যবহার করি। ঝাড়গ্রামের ভাষা, বীরভূমের ভাষা, বাঁকুড়ার ভাষা, কোচবিহারের ভাষা পরস্পরের থেকে খানিক আলাদা। এগুলির ঠিক কোনওটাতেই না লিখে স্কুল কলেজের বইপত্র বা সংবাদপত্র লেখা হয় কলকাতার মান্য বা প্রমিত বাংলা ভাষায়। পালি ভাষাও ছিল সেকালের এক মান্য বা প্রমিত প্রাকৃত ভাষা।
পালি বৌদ্ধধর্মের সূত্রে ভারতে ও ভারতের বাইরে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং অনেকগুলি পালি ব্যাকরণ রচিত হয়। ওয়াস্কারে সুব্বুতি তাঁর নামমালার ভূমিকায় ৪৫ টি পালি ব্যাকরণের নাম ও পরিচয় উল্লেখ করেছেন। এগুলির মধ্যে বেশি বিখ্যাত ছিল কচ্চায়ন, মোগ্গল্লান ও সদ্দনীতির রচিত তিনটি ব্যাকরণ।
এইবার চলে আসা যাক বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষাগুলি থেকে কোন কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষার জন্ম হল সেই আলোচনায়। এই প্রসঙ্গে যেটা বলার মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার কালপর্বটি অতি দীর্ঘ। ৬০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে ৯০০ খ্রিস্টাব্দ – প্রায় ১৫০০ বছর। এই দীর্ঘ পর্বে মধ্য ভারতীয় আর্য বা মিডল ইন্দো এরিয়ান তো একরকমের থাকে নি। তারও তিনটি আলাদা আলাদা স্তর দেখা গেছে। প্রথম স্তরটির নাম প্রাকৃত রাখা হয়েছে। এর আবার দুটি উপপর্ব আছে। প্রথম উপপর্ব হল অশোকের শিলালিপি স্তরের প্রাকৃত ও দ্বিতীয় উপপর্ব হল সাহিত্যে ব্যবহৃত প্রাকৃত। দ্বিতীয় স্তরটির নাম দেওয়া হয়েছে অপভ্রংশ। তৃতীয় স্তরটির নাম অবহট্ঠ। এই অবহট্ঠ পর্ব থেকেই আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির জন্ম হয়েছে।
কোন কোন অবহট্ঠ থেকে কোন কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষার জন্ম হল তার তালিকা নিচে রইলো –
মাগধী – বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরী।
অর্ধমাগধী – অবধী, বাঘেলী, ছত্তিশগড়ী।
পৈশাচী – সিন্ধী, পাঞ্জাবি।
শৌরসেনী – হিন্দি, উর্দূ, নেপালী, কুমায়নী, গাড়োয়ালি, হরিয়ানী, বুন্দেলী, কনৌজী, গুজরাটী, রাজস্থানী।
মাহারাষ্ট্রী – মারাঠী, কোঙ্কণী।
বাংলা ভাষার বয়েস হল হাজার বছর বা তারও খানিক বেশি। বেশীরভাগ পণ্ডিতের মতে খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দী নাগাদ প্রাচীন বাংলার জন্ম। সুনীতিকুমার চটতোপাধ্যায় এই মতের মূল প্রবক্তা। সুকুমার সেন, পরেশচন্দ্র মজুমদার, রামেশ্বর শ প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীরা এই মতটিকেই মেনে নিয়েছেন। তবে সুনীতিকুমারের সমকালীন ভাষাবিজ্ঞানী মহ শহীদুল্লাহ মনে করেছেন খ্রিস্টিয় আটশো শতাব্দী নাগাদই অবহট্ঠের জঠর ছেড়ে প্রাচীন বাংলা ভাষাটি আত্মপ্রকাশ করেছিল। হাজারই হোক বা বারোশ বছর – এই দীর্ঘ পর্বে বাংলা ভাষার উচ্চারণ, শব্দের গঠনের নিয়মে অনেক বদল এল। কালগত ধারায় বদল ছাড়াও রয়েছে স্থানিক বদল। বিরাট এক ভৌগোলিক এলাকা জুড়ে বাংলা ভাষায় আমরা কথা বলি। তার আঞ্চলিক রূপভেদ তাই অনেক। এই নিবন্ধ অবশ্য সে সম্পর্কিত নয়। এর আলোচনার বিষয় বাংলা ভাষার আদিতম চেহারার স্বরূপ। চর্যাপদ বইটিকে আশ্রয় করেই মূলত প্রাচীন বাংলার ভাষাবৈশিষ্ট্যকে নির্ধারণ করা হয়।
এই ভাষাবৈশিষ্ট্যকে কয়েকটি আলাদা আলাদা দিক থেকে আলোচনা করলে প্রাচীন বাংলা ভাষার সামগ্রিক চেহারাটি স্পষ্ট হবে। প্রাচীন বাংলার উচ্চারণ অর্থাৎ ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দের গঠন অর্থাৎ রূপতত্ত্ব, এর শব্দভাণ্ডার, শ্বাসাঘাতের প্রবণতা, ছন্দ, বাক্যের গঠন প্রভৃতি নিয়ে আমরা তাই আলাদা আলাদাভাবে কথা বলব।
(২)
ধ্বনিতত্ত্ব বা উচ্চারণ বিষয়ক কথাবার্তা
চর্যাপদের সময়কার বাংলা ভাষার আলোচনা শুরু করা যেতে পারে সে সময়ের ধ্বনির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের কথা দিয়ে। কয়েকটি ধ্বনি ও উচ্চারণ প্রবণতা নিয়ে কথা বলা যাক।
১) আমরা এখন অ স্বরধ্বনিকে যেভাবে উচ্চারণ করি হাজার বছর আগে সেভাবে এই ধ্বনি উচ্চারণ করা হত না। ধ্বনি উচ্চারণের সময় যদি মুখ অনেকটা খোলা থাকে, মুখের হাঁটা বড় হয়, তাকে বলে বিবৃত উচ্চারণ। আর যদি মুখটা অনেকটা ছোট হাঁ করে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে বলে সংবৃত উচ্চারণ। চর্যাপদে অ ধ্বনির উচ্চারণ ছিল অনেকটা বেশি বিবৃত। অনেকটা আ ধ্বনির কাছাকাছি। প্রশ্ন হল এটা বোঝা গেল কীভাবে। সেকালের ধ্বনির উচ্চারণ তো রেকর্ড করে রাখা নেই। আসলে এটা বোঝা যায় একটা পরোক্ষ প্রমাণ থেকে। সেটা একটু ব্যাখ্যা করা যাক।
আজকের দিনে আমাদের বানানে র/ড়, ন/ণ, শ/স, উ/ঊ মাঝে মাঝে গুলিয়ে যায়। তার একটা কারণ বর্ণ একাধিক থাকলেও উচ্চারণে এখনকার বাংলায় এইসব ধ্বনির তফাৎ নেই বা খুব সামান্য আছে। ফলে লেখার সময় সঠিক বানান না জানা লোক একই উচ্চারণের জন্য কখনো এই বর্ণ, কখনো ঐ বর্ণ ব্যবহার করে ফেলেন। এই ব্যাপারটা চর্যাপদের লিপিকাররাও ঘটিয়েছেন। একই ধ্বনি লেখার সময় কখনো অ বর্ণ ব্যবহার করেছেন, তো কখনো আ বর্ণ ব্যবহার করেছেন। যেমন – অইস/আইস, কবালী/কাবালী ইত্যাদি।
অ ধ্বনি বাংলায় বিবৃত উচ্চারণ থেকে ক্রমশ সংবৃত উচ্চারণের দিকে চলেছে এটা বোঝা যায়। চর্যাপদের সময়ে অ ধ্বনি অনেক বিবৃত এবং আ এর কাছাকাছি ছিল। আজকের দিনে অ ধ্বনি আবার বিপরীত প্রবণতা হিসেবে অনেকটা ও ধ্বনির মতো সংবৃতভাবে উচ্চারিত হচ্ছে। আমরা লিখি অতুল বা অগ্নি কিন্তু উচ্চারণ করি (বিশেষ করে রাঢ়ী উপভাষায়) ওতুল বা ওগ্নি।
২) এর পরে আসা যাক ল ধ্বনির উচ্চারণের ক্ষেত্রে। চর্যাপদে আনুনাসিল ল ধ্বনির উচ্চারণ ছিল। যেমন হেলেঁ। এই উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য ওড়িয়া ভাষার মধ্যে এখনো দেখা যায়। এরকম কিছু কারণে অনেকে চর্যাপদকে ওড়িয়া ভাষার আদিগ্রন্থ হিসেবেও তাই দাবি করেছেন। এই প্রসঙ্গে এটা মনে রাখা দরকার খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দী নাগাদ যখন চর্যাপদ লেখা হয়, তখন মাগধী প্রাকৃতের অবহটঠের স্তর থেকে পশ্চিমা ও পূর্বী শাখা পৃথক হয়েছে বটে, তবে পূর্বী শাখার ভাষাগুলো উপভাষা স্তর পেরিয়ে তখনো আলাদা আলাদা ভাষা হিসেবে পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠে নি। পূর্বী শাখার বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া তখনো অবধি পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ট বন্ধনেই ছিল। তাদের পৃথক যাত্রাপথটি দেখা দিচ্ছে তবে তা গঠনের স্তরেই আছে তখনো অবধি।
৩) এবারে আসা যাক হ ধ্বনির কথায়। শব্দের মাঝের বা শেষের হ ধ্বনির লোপের প্রবণতা এখনকার বাংলায় আমরা খুবই দেখতে পাই। যেমন বরাহনগর > বরানগর, খড়দহ > খড়দা, শিয়ালদহ > শিয়ালদা ইত্যাদি। চর্যাপদের সময়কার বাংলা ভাষার প্রবণতাটি কিন্তু হ ধ্বনিকে রক্ষা করে চলার। খুব প্রচলিত বাংলা সর্বনাম আমি বা তুমিকেও যে চর্যাপদে খানিকটা অচেনা লাগে তার কারণ আমি সেখানে আহ্মে, তোমার সেখানে তোহ্মার ইত্যাদি। হ ধ্বনির সংরক্ষণের এই বিষয়টি মাথায় রেখে পড়লে চর্যাপদ পাঠের সময় আধুনিক বাঙালি পাঠকের সেকালের শব্দ বোঝার অনেক জটিলতা কমে যাবে।
৪) এখনকার বাংলার সঙ্গে চর্যাপদের বাংলা উচ্চারণের অমিল যেমন আছে, তেমনি অনেক মিলও আছে। বৈদিক বা প্রাচীন ভারতীয় আর্যের যুক্তব্যঞ্জন মধ্য ভারতীয় আর্য বা প্রাকৃতের স্তরে যুগ্ম ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছিল। আধুনিক বাংলায় তা একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে। এই পরিবর্তন চর্যাপদের সময়েই শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং এই বৈশিষ্ট্য বাংলা ধ্বনির মৌলিক উচ্চারণ প্রবণতা হিসেবে এখনো বর্তমান আছে।
ধর্ম (বৈদিক) > ধম্ম (প্রাকৃত) > ধাম (প্রাচীন বাংলা)
তবে চর্যাপদ যেহেতু প্রাকৃতের অবহটঠ স্তর থেকে বাংলা ভাষার গঠনপর্বের অনেক রূপান্তরকালীন বৈশিষ্ট্যকেও ধারণ করে তাই প্রাকৃতের যুগ্মব্যঞ্জনও চর্যাপদের অনেক জায়গায় থেকে গেছে। যেমন বিমুক্কা, পুচ্ছমি, সূজ্জ, মিচ্ছা, মুত্তি ইত্যাদি। আধুনিক বাংলাতেও এরকম কিছু উচ্চারণ রক্ষিত। যেমন কর্তা > কত্তা। লৌকিক উচ্চারণে কত্তাবাবা কথাটি এখনো খুবই প্রচলিত।
৫) আধুনিক বাংলার, বিশেষ করে বঙ্গালি উপভাষার একটি প্রবণতা অপিনিহিতি। রাঢ়ী উপভাষাতে আবার অপিনিহিতির পরবর্তী ধাপ অভিশ্রুতির প্রবণতা ব্যাপক। চর্যাপদে অপিনিহিতির এই প্রবণতাটি দেখা যায় না। তবে আধুনিক বাংলার আর একটি প্রবণতা স্বরসঙ্গতি চর্যাপদে দেখা যায়। যেমন – শ্বশুর > সুসুরস, ঘেণেলি > ঘিনি ইত্যাদি।
৬) স্বরসংকোচ বা সন্ধি আধুনিক বাংলার একটি প্রবণতা। অন্যদিকে প্রাকৃতের স্তরে সন্ধির বিপ্রতীপ প্রবণতা স্বরসংযোগ বা পাশাপাশি দুটি স্বরের সংরক্ষণ দেখা যেত। এরকম পাশাপাশি দুটি স্বরের উপস্থিতি প্রাচীন বাংলা বা চর্যাপদের মধ্যেও ছিল। যেমন – চিঅরাঅ, করউ। আবার এর বিপরীতে স্বরসংকোচ বা সন্ধির উদাহরণও দেখা যায়। যেমন – করিঅ> করি, জাইউ > জাউ ইত্যাদি। মাগধী অবহটঠের স্বর থেকে আধুনিক বাংলার দিকে যাত্রাপথের ক্রমবদলের প্রক্রিয়াটি এইভাবে চর্যাপদ বা প্রাচীন বাংলার মধ্যে স্পষ্টভাবে ধরা আছে।
৭) এখনকার বাংলার আরেক বৈশিষ্ট্য য় শ্রুতি অর্থাৎ দুটি স্বরধ্বনি পাশাপাশি থাকলে মাঝে একটি য় ধ্বনি এসে যাওয়ার বৈশিষ্ট্য চর্যাপদে ভালোভাবেই দেখা যায়। যেমন নিঅডী > নিয়ড্ডী, জাঅ > জায়। ওয় শ্রুতি বা ব শ্রুতি অর্থাৎ দুটি স্বরধ্বনি পাশাপাশি থাকলে মাঝে একটি ওয় বা অন্তঃস্থ ব ধ্বনি এসে যাওয়ার বৈশিষ্ট্যও তখন বাংলায় প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে। যেমন রুঅ > রুব।
৮) নাসিক্য ব্যঞ্জনের সরলতা দেখা যায় চর্যাপদের স্তরেই। পূর্বস্বরের দীর্ঘিভবন ও আনুনাসিকতার প্রবণতা সে সময়েই বাংলা ভাষাতে আসতে শুরু করে। তবে এই বিষয়টি তখনো গঠনের স্তরে ছিল। সেটা বোঝা যায় চর্যাপদগুলিতে চন্দ/চান্দ, ভন্তি/ভাংতি এই দুই ধরনের শব্দের সহাবস্থানের মধ্যে দিয়ে।
৯) চর্যাপদে ই ও এ ধ্বনির বানান বিপর্যয় প্রচুর পরিমাণে আছে। মিলি/মেলে, ঘিণি/ঘেণি ইত্যাদি। এ থেকে অনুমান করা যায় ই কার অনেকটা শিথিলভাবে উচ্চারিত হয়, যাকে Lax উচ্চারণ বলা হয় ভাষাতত্ত্বে ই কারের তেমন উচ্চারণ সেকালের বাঙালি করত, চর্যার লিপিকরদের বানান বিপর্যয় তেমনই ইঙ্গিৎ দেয়।
১০) চর্যাপদে শ, ষ, স ইত্যাদিরো বানান বিপর্যয় প্রচুর। এ থেকে বোঝা যায় এখনকার বাংলার মতো সেকালেই তিনটি শ ধ্বনির উচ্চারণ পার্থক্য খুব কমে এসেছিল। একইভাবে ন/ণ ধ্বনির বিপর্যয়ও দেখা যায়। এই দুই ধ্বনির উচ্চারণ পার্থক্যও প্রাচীন বাংলাতেই প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়।
১১) প্রাচীন বাংলায় অন্তস্থ য ধ্বনি শব্দের আদিতে বর্গীয় জ হিসেবেই সম্ভবত উচ্চারিত হত। য এর তুলনায় বর্গীয় জ এর ব্যবহার বেশি দেখা যায় বানানে। যেমন – যোইয়া/ জোইয়া। শব্দ মধ্যবর্তী য ধ্বনি শ্রুতিধ্বনি হিসেবেই বেশি উচ্চারিত হত। সেখানে য/য় বানান বেশি দেখা যায়। তবে একটি ব্যতিক্রম দেখা যায়। ইন্দ্রিয়াণির বদলে পাওয়া গেছে ইন্দিজাণী শব্দটি।
১২) প্রাকৃত ও অপভ্রংশের স্তরে ঐ বা ঔ এর মতো যৌগিক স্বর ছিল না। অই, অউ এর মতো পাশাপাশি স্বরসংযোগ সেখানে দেখা যায়। প্রাচীন বাংলার স্তর এখান থেকে স্বরসংযুক্তির দিকে সরে আসে এবং ঐ ঔ এর মতো যৌগিক স্বর দেখা যায়। যেমন জৌবণ, চৌকোড্ডি ইত্যাদি।
(৩)
রূপতত্ত্ব বা শব্দের গঠন বিষয়ে কথাবার্তা
১) প্রাচীন বাংলার রূপতত্ত্ব বা morphology সংক্রান্ত কথাবার্তা লিঙ্গগত কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের আলোচনা দিয়ে শুরু করা যাক। চর্যাপদে শব্দের লিঙ্গভেদ নামপদ বা বিশেষ্য ছাড়াও সর্বণাম, বিশেষণ, কৃদন্ত বা সাক্ষাৎ বিশেষণ এবং সম্বন্ধবাচক বিশেষণের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়। নামপদে লিঙ্গ পার্থক্য সূচক শব্দ ব্যবহার যথেষ্ট। যেমন – হরিণা/ হরিণী, শবরা/ শবরী, চণ্ডাল/ চণ্ডালী, নরঅ/ নারী, কমল/ কমলিনী, করিণা/ করিণী ইত্যাদি।
২) কৃদন্ত বিশেষণে ল/লি পার্থক্য দেখা যায়। যেমন – পইঠেল গরাহক, বেঢ়িল হাক, মাতেল চিঅগঅন্দা ইত্যাদি পুংলিঙ্গ বাচক শব্দ। কিন্তু মেলিলী কাচ্ছী কাচ্ছী, ফিটেলী অন্ধারী, বুড়িলী মাতঙ্গী, সোনে ভরিলী করুণা নাবী ইত্যাদি হল স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ।
৩) সর্বনাম বিশেষণে লিঙ্গ পার্থক্যসূচক র/রি দেখা যায়। যেমন স্ত্রীলিঙ্গ বাচক তোহোরি কুড়িঅ, মেরি তইলা বাড়ী। কিন্তু পুংলিঙ্গ বাচক মোহোর বিগোআ, টালত মোর ঘর, জৌবণ মোর, জাহের বাণ ইত্যাদি শব্দ।
৪) সম্বন্ধ বাচক শব্দের ক্ষেত্রেও লিঙ্গ পার্থক্য দেখা যায়। এক্ষেত্রেও র/রি পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন স্ত্রী লিঙ্গ বাচক – চান্দেরি চান্দকান্তি, হাড়েরি মালী। আবার পুংলিঙ্গ বাচক রুখের তেন্তলি।
৫) ক্রিদন্ত ক্রিয়াপদেও ল/লি দিয়ে লিঙ্গ পার্থক্য সূচীত হত। যেমন স্ত্রী লিঙ্গ বাচক – সেজি ছাইলী, রাতি পোহাইলি, ঘেণিলি, টুটি গেলি কংখা, ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী। আবার পুংলিঙ্গ বাচক – চলিল কাহ্ন, জিতেল ভঅবল, ভইল উছারা, মিলিল মহাসুখসাঙ্গা ইত্যাদি।
৬) সাক্ষাৎ বিশেষণেও লিঙ্গ পার্থক্য ছিল। যেমন স্ত্রী লিঙ্গ বাচক প্রয়োগ – দিড়ি টাঙ্গী, নিশি অন্ধারী, একেলী শবরী, শবরী বালি ইত্যাদি। আবার পুংলিঙ্গ বাচক প্রয়োগ চঞ্চল মুসা।
৭) চর্যাপদে তথা প্রাচীন বাংলায় কেবল প্রাণীবাচক শব্দে নয়, গুণবাচক বা বস্তুবাচক শব্দেও লিঙ্গভেদ কল্পিত হত। চর্যায় জাতিবাচক পুংলিঙ্গ বাচক শব্দে অনেক জায়গায় আ প্রত্যয়ের ব্যবহার এক বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্যের সূচক। যেমন – হরিণা, করিণা, শবরা ইত্যাদি।
৮) এবার বচন সংক্রান্ত কিছু কথায় আসা যাক। চর্যায় বহুবচনের জন্য সমাসোত্তর পদ হিসেবে সমষ্টিবাচক শব্দ যোগ করা হত। যেমন পারগামি লোঅ, বিদুজণ লোঅ, কুলিণজণ, ইন্দিআল ইত্যাদি।
৯) শব্দের আগে বা পরে বহুত্ববাচক বিশেষণ যোগ করেও বহুবচন করা হত। যেমন – সকল সমাহিঅ, সঅল সহাবে, নানা তরুবর, বহুবিহ খেড়া, বিবিহ বান্ধন ইত্যাদি।
১০) সংখ্যাবাচক শব্দ যোগ করেও বহুবচন করা হত। যেমন – চউশঠী ঘড়িয়ে, পঞ্চ বি ডাল, চউউষঠ্ঠী পাখুড়ী।
১১) একই পদ দুবার ব্যবহার করে বহুবচন করার প্রবণতাও ছিল প্রাচীন বাংলায়। যেমন – উঁচা উঁচা পাবত, মিলি মিলি মাঙ্গা, জে জে আইলা তে তে গেলা ইত্যাদি।
১২) কর্তৃকারকে শূন্যবিভক্তি, ও বিভক্তি, এ বিভক্তির প্রয়োগ ছিল।
১৩) কর্মকারকে মুখ্য কর্মে শূন্য বিভক্তি, এ/এঁ বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়।
১৪) গৌণকর্মে এ/এঁ, ক/কে/কু, রে/রেঁ বিভক্তির প্রয়োগ ছিল।
১৫) করণ কারকে শূন্য বিভক্তি, এ/এঁ বিভক্তি, এতেঁ, ই(অ) বিভক্তির প্রয়োগ ছিল।
১৬) অপাদান কারকে শূন্য বিভক্তি, এ/এঁ, হু/হুঁ, ত বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়।
১৭) সম্বন্ধ পদে শূন্য বিভক্তি, আ, অহ, ক, এর, রি, করী বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়।
১৮) অধিকরণ কারকে শূন্য বিভক্তি, হি/হিঁ বিভক্তি, (অ)ই, এ/এঁ, ত, রে বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়।
১৯) প্রাচীন বাংলায় অপভ্রংশ অবহট্ঠসুলভ কিছু প্রাচীন বিভক্তির সংরক্ষণ দেখা যায়। যেমন – মায়-ও, ভান্তো, জো…সো, বোড়ো
২০) পুরনো বিভক্তির সংরক্ষণের দৃষ্টান্তের পাশাপাশি আধুনিক বাংলার মতো বিভক্তিহীনতা বা শূন্য বিভক্তির অনেক উদাহরণ চর্যাপদে দেখা যায়। যেমন কা আ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
২১) তির্যক বিভক্তি অর্থাৎ একই বিভক্তির নানা কারকে ব্যবহার চর্যায় দেখা যায়।
২২) বিভক্তির পরিবর্তে কোথাও কোথাও অনুসর্গের ব্যবহারও চর্যাপদে দেখা যায়। যেমন – তো এ সম, দুজ্জণ সাঙ্গে, ডোম্বীএর সঙ্গে, বিনা পাখেঁ, নিন্দ বিহুনে, দুধ মাঝেঁ, গঅণ মাঝেঁ ইত্যাদি।
২৩) আধুনিক বাংলায় চার ধরনের ক্রিয়াপদ দেখা যায়। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এবং নিত্যবৃত্ত। এর মধ্যে নিত্যবৃত্ত কালটির ক্রিয়াপদের উপস্থিতি প্রাচীন বাংলায় দেখা যায় না।
২৪) বর্তমান কাল বোঝাতে উত্তম পুরুষে ম, মি, হুঁ, অ, সি, অই, তি, থি ইত্যাদি বিভক্তি ব্যবহৃত হত। যেমন – অচ্ছম, জাণমি, জানহুঁ, আইসসি, অচ্ছহু, খাঅ, করিঅই, ভণতি, ভণথি ইত্যাদি।
২৫) বর্তমান কালের মধ্যেম পুরুষ বোঝাতে সি বিভক্তি তুচ্ছার্থে তুই জাতীয় শব্দে ব্যবহৃত হত। প্রথম পুরুষের ক্ষেত্রে অই, অএ, অঅ বিভক্তিগুলি ব্যবহৃত হত। যেমন – বাজএ, বাজঅ, বাজই ইত্যাদি।
২৬) অতীত কাল বোঝাতে চর্যায় ল প্রত্যয়যুক্ত ও ল প্রত্যয়হীন বিভক্তি – দুইরকমই দেখা যায়। বাংলা ভাষার নিজস্ব বিভক্তি হিসেবে ল বিভক্তিযুক্ত অতীতকে ধরা হয়। চর্যাপদে ল যুক্ত অতীত মূলত কর্তৃবাচ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। দেখিল, উভিল ইত্যাদি প্রয়োগ চর্যাপদে অনেক দেখা যায়।
২৭) ভবিষ্যৎ কাল বোঝাতে মধ্যম পুরুষে হসি (মারিহসি), ইহ (কহিহ) ইত্যাদি বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। ইব প্রত্যয় যুক্ত উত্তম পুরুষের ভবিষ্যৎ কালের উদাহরণ হল করিব ম সাঙ্গ, তুম্হে লোঅ হোইব পারগামী ইত্যাদি।
২৮) যৌগিক কালের উদাহরণ চর্যায় মেলে না, তবে যৌগিক ক্রিয়াপদের উদাহরণ বেশ কিছু আছে। যেমন – গুণিআ লেহুঁ, সড়ি পড়িআ, উঠি গেল, নিদ গেল, টুটি গেলি কংখা, দিঢ় করিঅ ইত্যাদি।
২৯) প্রাচীন বাংলায় কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যের প্রয়োগ যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। হরিণা হরিণীর নিলঅ ন জাণী। আখি বুজিঅ বাট জাইউ (কর্মবাচ্য)।
৩০) চর্যাপদে প্রযোজক ক্রিয়া বা ণিজন্ত ক্রিয়ার অনেক প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন – দেখইয়া, পতিআই ইত্যাদি।
(৪)
প্রাচীন বাংলার বাক্যরীতি, ছন্দ ও শ্বাসাঘাত
চর্যাপদের বাক্যগুলি ছন্দবিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে সেকালের মুখের ভাষার ছন্দনিরপেক্ষ স্বাধীন রূপটি এখান থেকে পুরোপুরি বোঝা সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও সেকালের বাক্যরীতি সম্পর্কে অনুমান করার কিছু উপাদান চর্যার পদগুলিতে রয়েছে।
১) চর্যার পদগুলি এক বা একাধিক সরল বা মিশ্র বাক্যের সমন্বয়ে গঠিত। সরল বাক্যের অনেক উদাহরণ রয়েছে। যেমন – হরিণা হরিণীর নিলঅ ণ জানী। কা আ তরুবর পঞ্চবি ডাল। আবার মিশ্র বাক্যও বেশ কিছু দেখা যায়। যেমন – জাহের বাণচিহ্ন রূপ ন জানী। সো কইসে আগম বেএঁ বখানী।। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় চরণটি প্রধান বাক্য, প্রথম চরণ তার বিশেষণধর্মী বাক্যাংশ।
২) মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার স্তর থেকেই প্রাচীন বিভক্তি ও প্রত্যয়গুলি লুপ্ত হয়ে আসছিল এবং তখন থেকেই বক্যগঠনরীতি সংহত না হয়ে ক্রমশ বহুভাষিত (peripharastic) হয়ে পড়ে। চর্যাপদেও এটা দেখা যায়।
৩) চর্যাপদে অনেক নঞর্থক বাক্যাংশ দেখা যায়। যেমন – ন পুচ্ছসি, ন জাই, ন ভুলই, ন দিঠা, ন হোই, ণ মেলই, মা দেসি, মা কর, মা জাহু, মা ভোল, ইত্যাদি।
৪) চর্যাকারদের সামনে দৃষ্টান্ত হিসেবে একদিকে ছিল অভিজাত সংস্কৃত ছন্দ ও অন্যদিকে লৌকিক অপভ্রংশ ছন্দ। চর্যাকাররা দ্বিতীয় ধরনের ছন্দরীতির দিকেই মূলত ঝুঁকেছেন।
৫) বিশেষ করে পাদাকুলক ছন্দ চর্যাপদে বেশি অনুসৃত হয়েছে। চর্যার সিংহভাগ, অন্তত ৩৬ টি পদ পাদাকুলক ছন্দের আদর্শে রচিত। তবে ৪+৪+৪+৪ ষোল মাত্রার পাদাকুলকের নিয়ম খানিকটা শিথিলভাবেই চর্যায় প্রযুক্ত হয়েছে।
৬) পাদাকুলক ছাড়া অপভ্রংশের দোহা, চউপইআ, চউবোলা, মরহাট্টা প্রভৃতি নানা দীর্ঘমাত্রার ছন্দও চর্যার কয়েকটি পদে দেখা যায়। ১০, ১৪, ১৫, ১৬, ২৩, ২৮, ৩৪, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৫০ সংখ্যক চর্যায় এই ধরনের দীর্ঘমাত্রার ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়।
৭) চর্যার ছন্দে এ কার, ও কার কখনো হ্রস্ব কখনো দীর্ঘ হিসেবে গণ্য করা হত। আ, ঈ, ঊ প্রভৃতি দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ কখনো কখনো হ্রস্ব বা একমাত্রার হত।।
৮) চর্যাপদে সাধারণত শব্দের প্রথম অক্ষরেই শ্বাসাঘাত থাকত। এটা ছন্দ থেকে বোঝা যায়। তবে শেষ অক্ষর দীর্ঘস্বরের হলে সেখানে শ্বাসাঘাত পড়ে। এর ফলে পূর্বের দীর্ঘস্বর অনেক সময় হ্রস্বস্বরে পরিণত হয়। যেমন হাথে (প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাত) কিন্তু হথা (শেষ দীর্ঘস্বরে শ্বাসাঘাত)।
(৫)
প্রাচীন বাংলার শব্দসম্ভার
১) আধুনিক বাংলায় সংস্কৃত শব্দের যে প্রাচুর্য দেখা যায়, চর্যাপদ থেকেই সেই ধারার সূচনা। যেমন – পঙচ, চঞ্চল, কুম্ভীর, গম্ভীর, অনুত্তর, কুন্ডল, তরঙ্গ, গঙ্গা, মাতঙ্গী। প্রতিতুলনা করে দেখা যায় দোহাকোষের মত অপভ্রংশ রচনায় এত সংস্কৃত শব্দ নেই। তৎসম ছাড়াও তদ্ভব শবও চর্যায় যথেষ্ট পরিমাণে আছে। অপভ্রংশের থেকে প্রাচীন বাংলার জন্মক্ষণের চিহ্ন এতে ধরা আছে।
২) অনেক সময় তৎসম ও অর্ধ তৎসম শব্দের পাশাপাশি ব্যবহার দেখা যায় চর্যায়। যেমন পুণ্য/পুণ্ণ, অলক্ষ/অলক্খ।
৩) অপভ্রংশ, অবহট্ঠের বানান পদ্ধতির বদলে সংস্কৃত বানানের আদর্শই চর্যায় গৃহীত হচ্ছিল। ণ স্থলে ন এর ব্যবহারের প্রবণতা চর্যায় বেশি। যেমন মোন স্থলে মন। মাগধী প্রাকৃতের শ বা অপভ্রংশে স এর জায়গায় চর্যায় শ, ষ, স – তিনেরই ব্যবহার দেখা যায়।
৪) চর্যাপদে একটি তুর্কি শব্দ দেখা যায়। সেটি হল ঠাকুর। তবে ১২ নং পদের এই শব্দটি সংস্কৃত সূত্র থেকেই এসেছিল বলে ভাষাবিদরা অনুমান করেছেন।
৫) মুণ্ডা ভাষা জাত শব্দ চর্যাপদের সময় থেকেই বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে। ডোম্বী, ডমরুর মতো শব্দ রয়েছে চর্যাপদে।
আকর
১) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় – অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ – রূপা প্রকাশনী
২) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ – বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত – মাওলা ব্রাদার্স (বাংলাদেশ)
৩) সুকুমার সেন – ক) ভাষার ইতিবৃত্ত খ) চর্যাগীতি পদাবলী – আনন্দ পাবলিশার্স
৪) পরেশচন্দ্র মজুমদার – বাঙলা ভাষা পরিক্রমা – দেজ পাবলিশার্স
৫) রামেশ্বর শ – সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা – পুস্তক বিপণি
৬) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী – হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা – বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
৭) শশিভূষণ দাশগুপ্ত – বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি – ডি এম লাইব্রেরী
৮) নির্মল দাশ – চর্যাগীতি পরিক্রমা – দেজ পাবলিকেশন
৯) নীলরতন সেন – চর্যাগীতিকোষ – সাহিত্যলোক
১০) ভারতীয় আর্য ভাষা – জুল ব্লখ – এবং মুশায়েরা

বেশ ভালো পড়ে।
বেশ ভালো লাগলো পড়ে।
দারুণ লাগল। ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা সহজে দেখা যায় না। এটি সেদিক থেকে একটা ব্যতিক্রমী লেখা। সংগ্রহে রাখলাম।
খুব প্রাঞ্জল ও তথ্য সমৃদ্ধ। ভালো লাগলো।
এই লেখার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, পচর্যাপদের পরবর্তী যুগেরও বাংলা ভাষা ও তার বিবর্তন নিয়ে আরও লেখা পড়তে ইচ্ছুক। লেখকেরও কাছে অনুরোধ এমন আর লেখা উপহার দেবার জন্য ।
Having lived in 64 destinations across India building projects with multi racial linguisric religious including Adi Vasis at Chaibasa etc, always felt how could Bhanu Bhakt was missed in Various stalwarts finding, but for my own clue with such Mahananda residents reciting Bhanu Bhakt amazed me.