
ডা. দিলীপ মহলানবিশ
সংক্ষিপ্ত জীবনী
ডা. দিলীপ মহলানবিশ ১৯৩৪ সালে ব্রিটিশ ভারতের বাংলা প্রদেশের কিশোরগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৮ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে তিনি ব্রিটেনে যান ও সেখানে চাকরি করতে করতে শিশুরোগ চিকিৎসার ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি দেশে ফিরে এসে কলকাতার জন হপকিন্স সেন্টার ফর মেডিকেল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং-এ যোগ দেন, এবং ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। ডা. মহলানবিশ আফগানিস্তান, মিশর এবং ইয়েমেনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কলেরা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীতে ১৯৭০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত কাজ করেছিলেন। ১৯৮০-র দশকে তিনি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের চিকিৎসা নিয়ে গবেষণায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শদাতা ছিলেন। ১৮৮৩ সাল থেকে পরের ৫ বছর তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডাইরিয়া-জাতীয় রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সদস্য ছিলেন। তিনি কলকাতার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কলেরা অ্যান্ড এন্টারিক ডিজিজেস (NICED) এবং ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথের সাথেও যুক্ত ছিলেন। ওরাল রিহাইড্রেশন সল্যুশন, সংক্ষেপে ওআরএস, হল ডা. মহলানবিশ ও অন্যন্য কয়েকজন বিজ্ঞানীর অনন্য কীর্তি। এতাবৎ কয়েক কোটি মানুষ, বিশেষত শিশুর প্রাণ বাঁচিয়েছে ওআরএস।
(১)
গত ১৬ অক্টোবর ২০২২, ডা. দিলীপ মহলানবিশ প্রয়াত হলেন। অনেকেই তাঁর নাম শোনেননি। ডাক্তার মহলানবিশ ছিলেন ডাইরিয়া ও কলেরা জাতীয় রোগে জীবনদায়ী চিকিৎসা মুখে খাবার দ্রবণ বা ওআরএস-এর অন্যতম আবিষ্কর্তা। আমাদের চোখের সামনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসের এক নায়ক কাজ করলেন, তারপর চলে গেলেন চোখের আড়ালে, আমরা বেমালুম ভুলে গেলাম। মৃত্যুর পরে অবশ্য তাঁর বাঙ্গালিত্ব নিয়ে চিরাচরিত চর্চা হল, নোবেল প্রাইজ দেওয়া উচিত ছিল কিনা সে নিয়ে তরজা হল। দুঃখের বিষয় বেঁচে থাকতে এই মনোযোগ বাঙালি বা ভারতীয় কেউই দেয়নি। রাষ্ট্র দেয়নি, তার দেবার দায় নেই। লৌহমানবের মূর্তি গড়ার মত বা স্কুলের ইউনিফর্মের রং ঠিক করে দেবার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিজ্ঞান নয়। ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ করে রাষ্ট্রের ইমেজ আরও ধারাল করে তুললে সে কদর পায়, কিন্তু তুচ্ছ রেফুইজি আর গরীবদের প্রাণ বাঁচিয়ে দায় বাড়ায় যে বিজ্ঞান তাকে রাষ্ট-বিরোধী বলে ঘোষণা করা না হলেই আমাদের অদৃশ্য আঙ্গুলিগুলো কচলানোর ইচ্ছে প্রবল হয়। যাক সে অপ্রিয় কথা।
কী করেছিলেন ডাক্তার মহলানবিশ? অন্য অনেক বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কাজ করে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন ওরাল রিহাইড্রেশন সল্যুশন, সংক্ষেপে ওআরএস। রাষ্ট্রসংঘের চিলড্রেন্স’ ফান্ড (ইউনিসেফ) এই ওষুধ সম্পর্কে বলেছে, “বিংশ শতকের আর কোনও একক মেডিক্যাল আবিষ্কার এত বেশি সংখ্যক মৃত্যুকে এত কম সময়ের মধ্যে এবং এত কম খরচে আটকানোর ক্ষমতা দেখায়নি।” না, পেনিসিলিনও নয়। হালফিলের যে সব ক্যানসার বা ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ নিয়ে মাতামাতি হয়, নোবেলও জোটে দু-একখান, সেগুলো এক গ্লাস জলে অল্প দামের খানিকটা পাউডার মিশিয়ে তৈরি ওআরএস-এর চাইতে ঢের বেশি প্রযুক্তি-সমৃদ্ধ। আমাদের ভক্তি তাদের প্রতিই। ঘরে বসেই বানিয়ে নেওয়া যায় এমন জিনিস—সেটা আবার ওষুধ নাকি! সে জিনিস তো আদ্যিকাল থেকে মানুষ খেয়ে আসছে, তার আবার আবিষ্কারক, তার আবার নোবেল! উন্নাসিক পণ্ডিতম্মন্যরা ভেবেই পান না কেমন করে তা হয়। শেষমেশ গবুচন্দ্র মন্ত্রীর ঢঙে ভেবে নেন, “মন্ত্রী কহে, “আমারো ছিল মনে—কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জানতে।”” (জুতা আবিষ্কার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
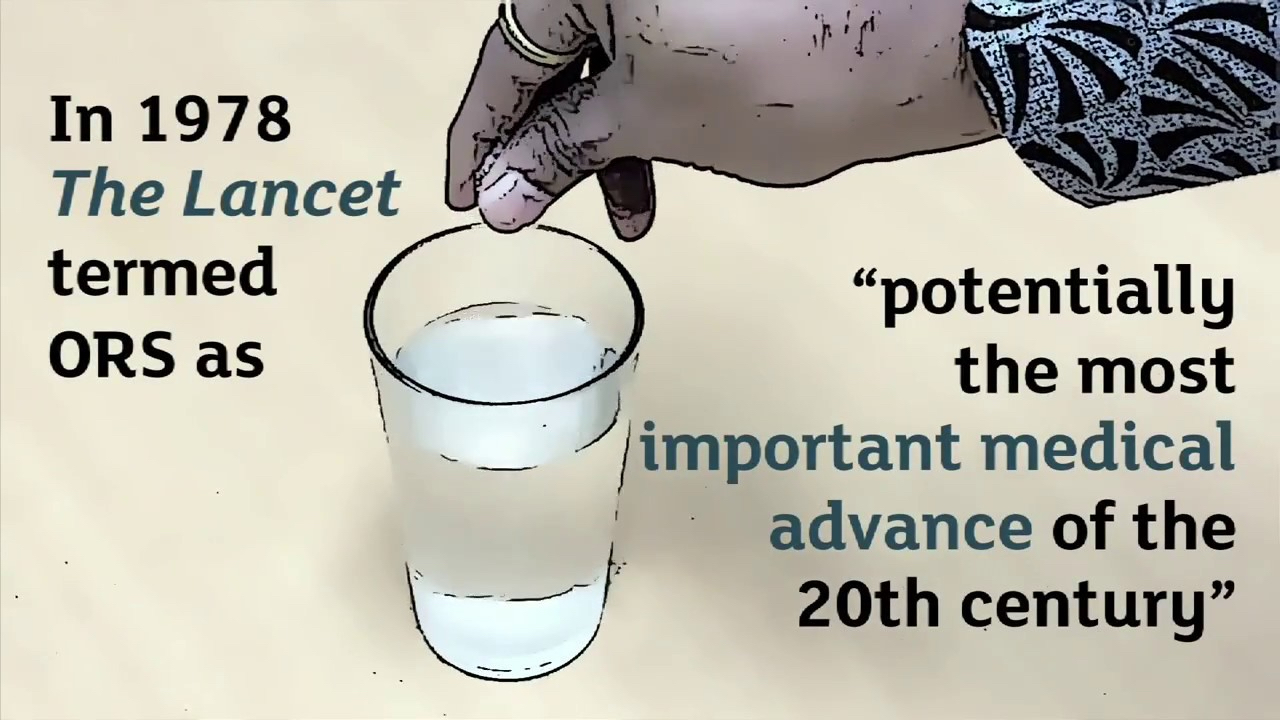
(২)
তখন ওলাউঠা হইলে সর্ব্বাঙ্গে ব্লিস্টার লাগাইত। তদনুসারে হেয়ারের গায়ে ব্লিস্টার দেওয়া হইয়াছিল। পরদিন অপরাহ্নে তিনি ধীরভাবে প্রসন্ন মিত্রকে বলিলেন—“প্রসন্ন! আর ব্লিস্টার দিও না আমাকে শান্তিতে মরিতে দেও!” (তথ্যসূত্র ১)
ওলাউঠা তথা কলেরায় আক্রান্ত হয়ে ডেভিড হেয়ার মারা যান ১৮৪২ সালে, তার পরের ১০০ বছর ধরে কলেরার চিকিৎসায় কিছু উন্নতি হলেও ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে মৃত্যুহার খুব কমেনি। তার কারণ হল, বাড়াবাড়ি ডাইরিয়া বা কলেরা—এসবের বাড়িতে করার মত চিকিৎসা কিছু ছিল না, উপরন্তু নির্জলা উপবাসের বিধান দেওয়া হত। একদিকে ডাইরিয়া ও বমিতে শরীর থেকে জল বেরিয়ে যাওয়া, অন্যদিকে মুখে কুটোটি না কাটা—শরীরের জল ও লবণের ভাণ্ডারে টান পড়ত। রোগীকে শেষ মুহূর্তে হাসপাতালে পাঠানো যদি বা সম্ভব হত, সেখানে একমাত্র চিকিৎসা ছিল শিরা ফুঁড়ে স্যালাইন। স্যালাইন হল লবণজল। কার শরীরে কোন লবণ কতটা কম পড়েছে, সে বিচার না করে লবণজল দেবার ফলে ভাল ফল যেমন হত, মন্দ ফলও কম হত না। ১৯৬০-৭০ সময়পর্বে বছরে কম-বেশি ৫০ লক্ষ শিশু ডাইবিয়া জাতীয় অসুখে মারা পড়ত—ছোট শরীরে লবণ ও জলের ঘাটতি সহজে হত, আবার স্যালাইন দিলে অতিরিক্ত লবণ বা জলকে শরীর থেকে চট করে বের করে দেবার পক্ষেও বাচ্চাদের দেহ অপরিপক্ক।
সেই সময়ের পুরো ব্যবস্থাটাই ছিল কাফকীয় দুঃস্বপ্নের মত। ১৯৬৮ সালে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে কলেরা নিয়ে কাজ শুরু করলেন ডাক্তার মহলানবিশ। তাঁর ভাষাতেই বলি —
“কলেরা ওয়ার্ডে তখন ঢুকতেন না ডাক্তাররা। নার্সরাও না। জনাকয়েক ওয়ার্ড বয় স্যালাইনের বোতল চালিয়ে দিত শিশুদের শরীরে। ওয়ার্ডে বাবা-মায়েদের ঢুকতে দেওয়া হত না, জানলার বাইরে তারা থাকতেন, ওয়ার্ড বয়রা তাঁদের শিশুদের তুলে ধরে দেখিয়ে দিত।” (তথ্যসূত্র ২)
ডাক্তার মহলানবিশের নেতৃত্বে এ-হেন হাসপাতালে গবেষণা শুরু হল। ইংল্যান্ড আমেরিকা বসে যারা একই গবেষণার অংশীদার ছিলেন, তাঁরা বোধ করি এতটা অব্যবস্থা কল্পনাতেও আনতে পারতেন না। তাঁরাই গবেষণার নিয়ম বানাতেন—কলোনিয়াল সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য ভরকেন্দ্রের নিয়ম বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমভাবেই খাটে। সেই আন্তর্জাতিক মানের গবেষণার নিয়ম অনুসারে চিকিৎসাধীন শিশুদের দুই দলে ভাগ করতে হল। তাদের এক দল পেল শিরা ফুঁড়ে স্যালাইন, তখনকার চালু চিকিৎসা। অন্য দলের বরাদ্দ ওআরএস। ওআরএস বলছি বটে, কিন্তু তখনকার ওআরএস-এর মিশ্রণ ছিল খানিকটা আলাদা, গবেষণার ফলে আজকের প্রমিত ওআরএস এসেছে। দু’দলের দু’রকম চিকিৎসা, তাতে কোন শিশুর কতটা উন্নতি-অবনতি হল, তার নিখুঁত খতিয়ান রাখা দরকার। এদিকে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালের নার্সেরা কলেরা-ডাইরিয়ার বাচ্চাদের মলমূত্র মাপার কাজ কখনও করেননি, গবেষণার খাতিরে করতে রাজিও নন তাঁরা। তাঁদের গবেষণাটির ব্যাপারে ধারণা নেই। ধারণা দিয়ে লাভও নেই, সরকারি জাবদা খাতার নিয়ম অথবা নিয়মহীনতার মাধ্যমে তাঁদের পোস্টিং-প্রোমোশনের গয়ংগচ্ছ চাকা চালু থাকে। অধিক খাটুনি খাটিয়া কী হইবে? বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত বা গবেষণার কাজে উৎসুক নার্সদের বেছে বেছে গবেষণাক্ষেত্রে পাঠানোর কোনও নিয়ম সেদিনও ছিল না, আজকেও নেই।
পড়াশুনো জানা কিছু ছেলেকে শিখিয়ে পড়িয়ে ওয়ার্ডে কাজের অস্থায়ী চাকরিতে বহাল করার ব্যবস্থা করলেন ডাক্তার মহলানবিশ। চাকুরিপ্রার্থীদের ইন্টারভিউতে তিনি সরাসরি বললেন, আমি যা যা করি সে সব তোমাদেরও করতে হবে। তারা রাজি হল, ঢুকল ওয়ার্ডে, মলমূত্র ঘেঁটে শিশুদের পরীক্ষা করতে হবে। সামনে থাকলেন ডা. মহলানবিশ। নিজে যা যা করতে পারেন না, অন্যকে তা করতে বলা তাঁর ধাতে নেই। মলমূত্র মাপতে শিখে গেল তারা, শিখল আরও নানা প্রয়োজনীয় কাজ।
এদিকে সরকারি ওয়ার্ড বয়দের নিয়ে হল ভারি সমস্যা। তারা বাচ্চাদের মা-বাবাকে শুধু রোগী দেখাত তাই নয়, শিশুদের অবস্থা সামান্য ভাল হলেই বাবা-মায়ের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে রোগী ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করত তারা। বাচ্চা ঘরে গিয়ে বাঁচল কি মরল সে দায় বাপ-মায়ের। একদিকে রোগীর ক্ষতি, অন্যদিকে গবেষণাধীন রোগীদের ওপর সমস্ত মাপজোক শেষ হবার আগেই তারা বাড়ি যাবার ফলে গবেষণা পণ্ড হতে বসল। ডাক্তারবাবুর অনুরোধ-উপরোধে লাভ হল না, বহুদিনের প্রথা চালু থাকায় সরকারি মাইনের ওপরে কাঁচা পয়সাটা ওয়ার্ড বয়দের পাওনা হয়ে গেছে। নতুন রিক্রুট দুটি রোগা-প্যাংলা ছেলে বলল, ডাক্তারবাবু, আমাদের ওপর ছেড়ে দিন। তারা ষণ্ডাগুণ্ডা ওয়ার্ড বয়দের গিয়ে বলল, নিয়ম ভেঙে রোগী ছাড়লে লাশ ফেলে দেবে। সেই সময়ে বেলেঘাটা তখন রোগা-প্যাংলা ছেলেদের দখলে। মাস্তান ওয়ার্ড বয়রা রোগী ছাড়া বন্ধ করে দিল। কিন্তু এ যে ঘোর অনাচার! প্যাংলা ছেলে দুটির একজনের লাশ ক’দিন পরেই পুলিশই ফেলে দিল। তারা ছিল নকশালপন্থী। এইসব দধিচীর হাড় দিয়ে দৈত্যদানো মারার বজ্র শেষ পর্যন্ত গড়া যায়নি, কিন্তু মানুষকে বাঁচানোর ওআরএস গবেষণার কাজে তার অবদান কম ছিল না।
১৯৭০ সালে আমেরিকান জার্নালে পাঠানো হল গবেষণাপত্র। ডা. মহলানবিশ দেখালেন, আন্ত্রিক বা কলেরা হলেও রোগীর পরিপাকতন্ত্র লবণ ও চিনি মেশানো জল শোষণ করতে পারে। এটাই ছিল ওআরএস-এর তাত্ত্বিক ভিত্তি। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের অখাত গবেষকের গবেষণাপত্র, পড়ে রইল বছরভর।

ঢল নামছে সীমান্ত পেরিয়ে আসা উদ্বাস্তুর
ওআরএস-এর জন্ম পাশ্চাত্যের গবেষণাগারে নয়, এমনকি বেলেঘাটার হাসপাতাল ও বাংলাদেশের হাসপাতাল তার প্রকৃত জন্মস্থান হয়তো নয়। যখন বেলেঘাটায় মস্তানদমন চলছে তখন পূর্বদিকে চলছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ঢল নামছে সীমান্ত পেরিয়ে আসা উদ্বাস্তুর। ক্যাম্পে হানা দিচ্ছে কলেরা। মরছে মানুষ পিঁপড়ের মত। সেখানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার অস্ত্রটিও আবিস্কৃত ও পরীক্ষিত হয়ে গিয়েছিল, এমন বললে ভুল হবে না। সীমান্তের পাশে বনগাঁ ক্যাম্পে পাঠানো হল ডা. মহলানবিশকে, সেখানে চলছিল কলেরার মড়ক।

সীমান্তের পাশে বনগাঁ ক্যাম্প
ইন্দিরা গান্ধি তখন ক্যাম্পে বিদেশি প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন বলে আমেরিকান গবেষকেরা ক্যাম্পে ঢুকতে পারলেন না। হয়তো সেটা ভালই হয়েছিল, ডা মহলানবিশ নিজের বিবেচনামাফিক কাজ করতে পারলেন। ডাক্তারবাবু দেখলেন, বন্যার মত মানুষ ক্যাম্পে আসছে, তাদের রাখার স্থান দেওয়াই দুরূহ ব্যাপার। সেখানে শিরা ফুঁড়ে স্যালাইন দেবার মত ব্যবস্থা করা কার্যত অসম্ভব। ওআরএস ছাড়া গতি নেই। বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে গ্লুকোজ, নুন আর সোডি-বাই-কার্ব মিশিয়ে ওআরএস-এর শুকনো প্যাকেট তৈরি করে পাঠানো হতে লাগল বনগাঁ ক্যাম্পে। সেখানে ১৬ লিটার ড্রামে করে জল নিয়ে তাতে মেশানো হল একটা করে প্যাকেট। অবশ্য শিরা ফুঁড়ে স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে না বলে বিক্ষোভও করেছিল রোগীদের কেউ কেউ। ডা. মহলানবিশ বললেন, এটা হল মুখে খাবার স্যালাইন। আপত্তি, এমনকি বিক্ষোভ চলল কিছুদিন। এসবের মধ্যে লোকে দেখল, শিরা ফোঁড়া হোক না-হোক, ঐ ভয়ানক নরকযন্ত্রণার মধ্যেও পেটের গণ্ডগোলে মৃত্যুহার কমছে। তারা গ্রহণ করল এই ওষুধকে, বমি করতে করতেও ওআরএস গোলা জল খেতে চেষ্টা করতে থাকল। মানুষ বাঁচতে বড় ভালবাসে।
ওআরএস–এর ফর্মুলা সহজ। আবিষ্কারের ইতিহাস মোটেই সহজ নয়। কয়েকজন বিজ্ঞানী ব্যক্তিগত লাভক্ষতি, অর্থ বা খ্যাতির হিসেব করেননি। ডা. মহলানবিশ ছিলেন তাঁদের একজন। তাঁকে মনে রাখার কোনও কারণ স্বভাবতই আজকের বাঙালি খুঁজে পাবে না, তিনি নিজের ঢাক বাজাতে ঘৃণা করতেন। তবে ওআরএস-এর স্বার্থে, রোগীদের স্বার্থে, তিনি লড়াই চালাতে পিছপা ছিলেন না। সে লড়াই চলেছে ক্যাম্পে-হাসপাতালে, জার্নালে-কনফারেন্সে। বিশ্বখ্যাত দু-একজন বিজ্ঞানী সুবিধাজনক অবস্থানের জোরে একগুঁয়েমি করে এর পথ আটকানোর চেষ্টা করেছিলেন, তাই আকাদেমিক লড়াইটাও খুব জরুরি ছিল।
(৩)
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে রোগের জার্ম থিয়োরি চালু হবার পরে বিংশ শতকের গোড়ায় তা প্রাতিষ্ঠানিক ডগমা হয়ে বসে। তখন থেকে নানারকমের ডাইরিয়া ও কলেরার গবেষণাতে রোগের জীবাণু খুঁজে বের করা ও তাকে মারার মাধ্যমেই রোগ সারানোর চেষ্টা করা হতে লাগল। কিন্তু কলেরা বা যে কোনও ডাইরিয়ায় শরীরের জল বেরিয়ে যাবার ফলে রোগী মরে। এটা অনেক বিজ্ঞানী বুঝলেন, এবং জীবাণু মারা হোক বা না-হোক, তাঁরা শিরা ফুঁড়ে স্যালাইন বা লবণ জল দিয়ে জলশূন্যতার চিকিৎসা করতে শুরু করলেন। তবে তখন সবার একটা ভাবনায় মিল ছিল—ডাইরিয়ার সময়ে আমাদের পরিপাকনালীর খাদ্যগ্রহণ ক্ষমতা থাকে না, তাকে মুখে কিছু খাওয়ানো ক্ষতিকারক। রোগীদের উপোষ করিয়ে শিরায় নানা রকমের স্যালাইন ধরনের তরল চালিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল, তাতে মৃত্যুহার কিছুটা কমে।
কিন্তু ডাইরিয়া আক্রান্ত রোগীদের বড় অংশ ছিল শিশু, তাদের কিছুদিন উপোষ করিয়ে রাখার ফলে তারা অপুষ্টির শিকার হত। ডাইরিয়ায় না মরলেও তারা পরে অপুষ্টি জনিত রোগে মারা যেত। তাছাড়া স্যালাইন দেবার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করতে হত, তাতে চিকিৎসা শুরু করতে দেরি হত, আর খরচ হত বেশি। এর ওপরে আবার ঠিক কোন ধরনের স্যালাইন দেওয়া হবে, কীভাবে রোগীদের অবস্থা বোঝা যাবে, এ নিয়ে ঐক্যমত্য ছিল না। ফলে বিভিন্ন হাসপাতাল ডাক্তারেরা ভিন্নভাবে চিকিৎসা করতেন। যে সব রোগী ভর্তি হত তাদের অর্ধেকই মারা যেত।
১৯৪০ সালে ডাক্তার ড্যানিয়েল ডারো নানারকমের ডাইরিয়া রোগীর ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নানা লবণ নির্দিষ্ট মাপে দিয়ে এক প্রমিত মানের স্যালাইন বানালেন। ডাইরিয়ার চিকিৎসা অনেকটা বিজ্ঞানসম্মত হল, উন্নত দেশগুলোতে মৃত্যুহার কমল। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয় ডারো সাহেবের স্যালাইন চালানোর উপযুক্ত হাসপাতাল, যথেষ্ট চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী ছিল না। রোগীরা শেষ অবস্থায় হাসপাতালে পৌঁছাত। তাই সেখানে মুখে খাবার ওষুধ ছাড়া বড় পরিবর্তন সম্ভব ছিল না। কিন্তু তখন অধিকাংশ বিজ্ঞানী ভাবতেন, ডাইরিয়ায় পরিপাকনালীর কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।
১৯৫০-এর দশকে ইঁদুরের অন্ত্রে গ্লুকোজের উপর নির্ভরশীল সোডিয়াম ও জল শোষণের পদ্ধতি আবিষ্কার হয়। তারপরে ডাইরিয়ার চিকিৎসায় গ্লুকোজের সঙ্গে লবণজল খাওয়ানোর কথা ভাবা হয়। বিজ্ঞানের জগতে আরেকজন বাঙালি এখানে বড় অবদান রেখেছিলেন—হেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ১৯৫৩ সালের ল্যানসেট-এ তাঁর গবেষণা প্রকাশিত হয়। তিনি কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে দেশিয় ভেষজ ওষুধ ও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ওষুধ খাইয়ে রোগীর বমি বন্ধ করে, তারপর মুখে লবণ ও গ্লুকোজের দ্রবণ খাইয়ে অনেক রোগীকে রোগমুক্ত করেছিলেন। অবশ্য কলেরা-ডাইরিয়া গবেষকদের মধ্যে হেমেন্দ্রনাথ প্রথম কাব্যে ও স্বদেশে উপেক্ষিত নন। কলেরার রোগী যে জলশূন্যতায় মরে যায়, কলেরা জীবাণুর দেহনিঃসৃত কোনও বিষ বা টক্সিনের প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার ফলে মারা যায় না, সেটা প্রথম প্রমাণ করেছিলেন আরেকজন বাঙালি। তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের আরেকজন প্রতিভাবান ও মুখচোরা ছাত্র, ডাক্তার শম্ভুনাথ দে। ১৯৫৯ সালে ‘র্যাবিট লুপ মডেল’ ব্যবহার করে তিনি দেখিয়েছিলেন, তখনকার চালু ভাবনা ‘কলেরা টক্সিনের কারণে রোগীমৃত্যু’ একটি ভুল ধারণা। নোবেল পেতে পারতেন শম্ভুনাথ, তাঁর নাম বেশ কয়েকবার সুপারিশ করেছিলেন নোবেলজয়ী কিছু বিজ্ঞানী। তিনি নোবেল সিম্পোসিয়ামে তাঁর কাজ নিয়ে বক্তৃতার ডাকও পান, কিন্তু সে অনেক পরে। বাঙালি যথারীতি তাঁকেও ভুলে মেরে দিয়েছে। অবশ্য বেঁচে থাকতেও এই দুজনের একজনকেও যথাযথ স্বীকৃতি দূরস্থান, কাজ করার অনুদানটুকুও দেয়নি কেউ। আমরা মহান জাতি!
১৯৬১ সালে ফিলিপিন্সে কলেরা মহামারীতে ডাক্তার রবার্ট ফিলিপ্স গ্লুকোজ ও লবণজলের মিশ্রণ খাইয়ে কিছু কলেরা রোগীকে সুস্থ করে তোলেন। এরপরে বড় মাত্রায় পরীক্ষা করতে গিয়ে কয়েকজন কলেরা রোগীর মারা যায়, ও তিনি পরীক্ষা বন্ধ করে দেন। পানীয়ে গ্লুকোজ ও লবণের মাপ ঠিক ছিল না। ডাক্তার ফিলিপ্স ভুল বুঝে বিজ্ঞান পত্রিকায় লেখেন, কলেরার সময় পরিপাকনালীর ক্ষমতা কমে যায়, তাই এর একমাত্র চিকিৎসা শিরার মাধ্যমে স্যালাইন। পেছনপানে উল্লম্ফনের একটি ধাপ সম্পূর্ণ হল।
(৪)
১৯৬০ সালে ঢাকায় পাকিস্তান-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় একই সময়ে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় দ্য জন হপকিন্স সেন্টার ফর মেডিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড ত্রেনিং। দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীদের নিয়ে জোরকদমে কলেরা-ডাইরিয়া নিয়ে গবেষণার কাজ চলল দুই জায়গাতেই। ঢাকার কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ডেভিড সাচার তাঁর বাঙালী সহযোগী চিকিৎসকদের সঙ্গে পরীক্ষায় প্রমাণ করেন, কলেরা রোগীদের খাদ্যনালীর গ্লুকোজনির্ভর সোডিয়াম শোষণের ক্ষমতা নষ্ট হয় না। কথাটা একটু জটিল। আমাদের খাদ্য লবণ হল সোডিয়াম ক্লোরাইড। জলীয় দ্রবণে তা সোডিয়াম ও ক্লোরিন আয়ন তৈরি করে। ডাইরিয়া-জাতীয় রোগে মৃত্যুর একটা বড় কারণ হল শরীরে সোডিয়াম ঘাটতি। মুখে কেবল লবণ দিলে তার সোডিয়াম আয়ন শরীরে তাড়াতাড়ি ঢুকতে পারে না, লবণের সঙ্গে গ্লুকোজ দেওয়া দরকার। গ্লুকোজ সোডিয়াম আয়নকে অন্ত্রের মাধ্যমে দেহে ঢুকতে সাহায্য করে। তাছাড়া গ্লুকোজ পুষ্টি জুগিয়ে পরে বাচ্চাদের অপুষ্টিতে ভোগার সম্ভাবনা কিছুটা কমায়।
এক কথায়, সাচার-রা দেখালেন, কলেরা রোগীদের মুখে গ্লুকোজ-লবণজল খাইয়ে জলশূন্যতা সারানো সম্ভব। কলকাতার চিকিৎসকেরাও একই ব্যাপার দেখতে পান। কিন্তু বিদেশের বড় বড় কেন্দ্রের চিকিৎসক-বিজ্ঞানীরা এটা মেনে নিতে পারলেন না। ফিলিপিন্সে ডা. রবার্ট ফিলিপ্স যে বলেছিলেন, কলেরা হলে পরিপাকতন্ত্র কিছু শোষণ করতে পারে না, সেটাই সম্ভবত অতিরিক্ত গুরুত্ব পেয়ে গিয়েছিল। আমেরিকান আকাদেমি অফ পেডিট্রিশিয়ানস নাকচ করেছিল ওআরএস-কে। কে না জানে আমেরিকানদের সর্দি লাগলে বাকি চিকিৎসক-বিশ্ব বেজায় হাঁচতে শুরু করে! বারংবার এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে ডা. মহলানবিশ ও অন্যান্য ওআরএস আবিষ্কারকদের। আসল কথাটা বেরল পরে—ডা. রবার্ট ফিলিপ্স তাঁর দ্রবণে লবণ বেশি দিয়েছিলেন। সেটা একটা বিশেষ ওআরএস ফর্মুলার ব্যর্থতা, সমস্ত ওআরএস-বিজ্ঞান তার জন্যে বাতিল হয়ে যায় না। কিন্তু প্রথমদিকে এসব কারণে কলকাতায় বা ঢাকায় রোগীদের ওপর ওআরএস নিয়ে চিকিৎসার অনুমতি মেলেনি।
দিলীপ মহলানবিশ একা কুম্ভ ছিলেন না। চট্টগ্রামে কলেরা মহামারীর সময়ে ডাক্তার রফিকুল ইসলাম সেখানে ওআরএস দিয়ে কলেরার চিকিৎসা করে অনেক রোগীকে সুস্থ করছিলেন। তাঁদের চিকিৎসা পদ্ধতির নাম দেওয়া হয় ‘ইসলাম প্রোটোকল’। দুই আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ডেভিড নালিন ও রিচার্ড ক্যাশ সেখানে যান। যথেষ্ট নথিপত্র রাখা হয়নি, এই কারণে পশ্চিমি চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা শেষ পর্যন্ত এই প্রটোকলকে বিচার করতে রাজি হননি। অভিযোগটি পুরো ভিত্তিহীন নয়। তবে পরে বোঝা গেল, ‘ইসলাম প্রোটোকল’ কাজ করে। তখন ডাক্তার রফিকুল ইসলাম বলেছিলেন, জীবন বাঁচানো ছিল আমার কাজ, আমি করেছি। পরিকাঠামো অল্প ছিল, তাই নিয়ে নথিপত্র রাখা শক্ত ছিল, স্বীকৃতি পাইনি। আমার দুঃখ নেই। চট্টগ্রামের চাঁদপুর জেলার ‘মতলব’ হাসপাতালে ডাক্তার মিজনুর রহমান ওআরএস দিয়ে কলেরা রোগীদের চিকিৎসার অনুমতি ছাড়াই ওআরএস দিয়ে চিকিৎসা করে অনেক রোগীকে বাঁচান। তাঁর বক্তব্য ছিল, অনুমতি নেই বলে তো জেনেশুনে চোখের সামনে রোগীদের মরতে দিতে পারি না।
যাই হোক, নানান বাধা পেরিয়ে ঢাকা কলেরা রিসার্চ ল্যাবোরেটরির প্রধান ডাক্তার হেনরি মসলে-র সহযোগিতায় নালিন ও ক্যাশ-এর প্রটোকল ছাড়পত্র পায়। ওআরএস নিয়ে ঢাকায় তাঁদের ট্রায়াল সফল হয়। একই সময়ে ডাক্তার মহলানবিশের নেতৃত্বে কলকাতার তথা বনগাঁ শরণার্থী শিবিরের ট্রায়াল সফল হয়। শুধুমাত্র ওআরএস দিয়ে ও হাসপাতালে ভর্তি না করেও কলেরার মৃত্যুহার অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব হয়।
ডাক্তার মহালনাবিশের নিজের ভাষায়, “আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেন, ওআরএস চিকিৎসা কোথায় প্রথম প্রমাণিত হয়েছিল, ঢাকা না কলকাতা। আমি বলি, ঢাকাতে ও কলকাতায় একসঙ্গে কাজ হয়েছিল, কিন্তু যে ভাবে ‘র্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়াল’-এর প্রতিটি নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, প্রতিটি শিশুর প্রতিটি প্রয়োজনীয় তথ্য রেখে কলকাতায় গবেষণা হয়েছে, তা হয়নি ঢাকায়।” (তথ্যসূত্র ২)
ওআরএস এর ফর্মুলায় কিছু কার্যকর পরিবর্তন করেন ডা. মহলানবিশ। তিনি বেশ কিছু আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন, ২০০২ সালের পলিন পুরস্কার তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমেরিকা বা ইউরোপের নাগরিক হলে তিনি আরও বেশি পুরস্কৃত ও স্বীকৃত হতেন। তবে বাংলার মানুষই তাঁকে আরেকটু সম্মান দিতে পারত বলেই মনে হয়। অথবা তার জন্যও হয়তো প্রথম বিশ্বের নাগরিকত্ব লাগে!

বেলেঘাটা আইডি হাসপাতাল
চলে গেলেন তিনি। বনঁগার ক্যাম্প আর নেই, কিন্তু তাঁর বেলেঘাটা আইডি হাসপাতাল আর নাইসেড পড়ে রইল। তাঁকে নিয়ে লোকে ভাববে, তেমন আশা দেখি না। চারিদিকে কার্নিভাল আর দেওয়ালির উৎসবে মত্ত কলকাতা পড়ে রইল। রত্নগুলো ধুলোয় ফেলে আঁচলে কানা পয়সা গিঁট দেওয়া মানুষ আরও কষে গিঁট বাঁধল। এদেশ তো এমনি এমনি দরিদ্র হয়নি!
তথ্যসূত্র
১) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। শিবনাথ শাস্ত্রী (প্রথম প্রকাশ ১৯০৩)। নিউ এজ; তৃতীয় সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৯৮৩, পৃ ১৫১
২) শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ওষুধ: দিলীপ মহলানবিশ এবং ও আর এস। চক্রব্যূহে বৈজ্ঞানিক। স্বাতী ভট্টাচার্য। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স; পৌষ ১৪১২

এমন সহজ অথচ তথ্যসমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য অশেষ ধন্যবাদ।
কেবল ব্লিস্টার ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দেবেন??
ব্লিস্টার ব্যাপারটা হল, গরম কিছু দিয়ে ফোস্কা ফেলে চিকিৎসা। ডেভিড হেয়ারের গায়ে ঠিক কোন্ জিনিসটা দিয়ে ফোস্কা ফেলা হয়েছিল জানা নেই। সেই সময়ে কোনো তেলের, যেমন সর্ষের তেল, গরম পুলটিস লাগিয়ে ব্লিস্টার করা হত।
আসুরিক চিকিৎসা, কথাটা সাধে বলা হত না। ব্লিস্টার প্লাস্টার আর রক্তমোক্ষণ – এসব পাশ্চাত্য চিকিৎসার অঙ্গ ছিল।